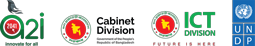- ইউনিয়ন সম্পর্কিত
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ..
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
-
সরকারি অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য
সমাজসেবা
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
-
বিভিন্ন তালিকা
সুবিধাভোগীদের তালিকা
মহিলা বিষয়ক
সমাজসেবা বিষয়ক
আরো .....
- প্রকল্প সমূহ
- সেবা সমূহ
-
গ্যালারি
-
লিগ্যাল এইড
-
ক্রয় পরিকল্পনা
-
ইউনিয়ন সম্পর্কিত
ইউনিয়ন পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ভৌগলিক অবস্থান
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ..
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
-
সরকারি অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য
সমাজসেবা
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
-
বিভিন্ন তালিকা
সুবিধাভোগীদের তালিকা
মহিলা বিষয়ক
সমাজসেবা বিষয়ক
আরো .....
- প্রকল্প সমূহ
-
সেবা সমূহ
কিকি সেবা পাবেন
রেজিষ্টার সমূহ
-
গ্যালারি
-
লিগ্যাল এইড
-
ক্রয় পরিকল্পনা
বহমান সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন। জীবন যাত্রার গহীনের ভেতর লুকিয়ে আছে চিরন্তনি লোকায়ত মর্ম বেদনার সুর। সে সুরের বেসুরো লয়তালে আমাদের চোখের সামনে মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে। মায়াবি পর্দার ম্যাজিক লন্ঠনের মতো আমাদের মনে দোলা দিয়ে যায় চির বহতা লোক সংস্কৃতির বকুল বাতাস। রবীন্দ্র নাথের ভাষায় বলতে হয় আমরা সে সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির আড়ালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও সে বাগানের অলি যে বারবার ফিরে আসে আমাদের পরানের গহীনে।
প্রথমত আমার ধারনা এই লোক সংস্কৃতি আখ্যায়িত করে আমাদের শোনিত ধারায় চিরন্তনি আবাহন সংস্কৃতিকে কী বৃত্তাবদ্ধ করা হচ্ছে? সংস্কৃতির বিশাল ভান্ডারের আকাশ হলো অসীম। এই অসীম ভান্ডারের ভেতরেই বাংগালির দৈনন্দিন জীবন। লোক সংস্কৃতির বৃত্তাবদ্ধকে উম্মোচন করে আমরা কী আখ্যায়িত করতে পারিনা লোক সংস্কৃতি নয় বরং আবহমান বাংগালির সংস্কৃতি জীবন? প্রশ্নটি রেখে গেলাম, একটি সঠিক উত্তরের আশায়।
ঐতিহাসিক জনপদ হিসেবে গৌরবজ্জল সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী প্রাচীন জনপদ সোনারগাঁও, একথাটি বলার অপেক্ষা রাখেনা। দীর্ঘ কয়েকশত বছর কখনো পূর্নাঙ্গ রাজধানী কখোনাবা প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের গর্ব কিংবদন্তিতুল্য। সভ্যতার বিলীয়মান অস্তিত্বের রূপরেখায় সোনারগাঁও পর্যবসিত হয়েছে বাংলাদেশের হাজারো গ্রামের মতো বেশ কয়েকটি গন্ড গ্রামে। সমৃদ্ধশালী নগর জনপদের ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে ঐ গন্ড গ্রামগুলোতে। এখন অবশ্য নগর সভ্যতার বিবর্তনে গ্রাম আর গ্রাম নেই। সেখানে এখন জোনাকী জ্বলেনা, জ্বলে বৈদ্যুত্যিক আলো। এ গ্রাম গুলোর অস্থিমজ্জার ভেতর সোনার গাঁয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য লুকিয়ে থাকার পাশাপাশি লুকিয়ে আছে সমৃদ্ধ লোকজ শিল্পের এক বর্নাঢ্য ইতিহাস। ইতিহাসের ভেতরের নেপথ্যের লুকায়িত লোকজ উপাদানের ইতিহাসকে খুঁজে বের করারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস বক্ষ্যমান এই নিবন্ধটি। এই নিবন্ধটিতে আমরা গ্রামগুলোর একটি সারিবদ্ধ ইতিহাস এবং লোকজ উপাদানের ছাঁচে গড়ে তুলতে পারি সম্ভবত এটিও একটি গ্রাম ভিত্তীক লোকজ শিল্প উপাদান খোঁজার এক মহতি প্রচেষ্টা। ইদানিং কালের লুপ্তপ্রায় কয়েকটি বন্দর ইউসুফগঞ্জ, কাবিলগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ এবং উদ্ধবগঞ্জ বন্দর এবং বন্দর নামগুলো লোকজ শিল্প সম্ভারের রফতানির জন্যে ব্যবহৃত নাম বলেই ধারনা করা যায়। ইউসুফ গঞ্জ বন্দর সৈয়দ হযরত মোঃ ইউসুফের নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাবিলগঞ্জ বন্দর সৈয়দ হযরত মোহাম্মদ কামেল শাহ এবং কোম্পানিগঞ্জ বন্দর ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সোনার গাঁয়ের বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র ইউরোপে রফতানির বন্দর হিসেবে স্বীকৃত। নবীগঞ্জের কাছাকাছি বন্দর সুলতানি আমল থেকেই সোনার গাঁয়ের চারু ও কারু শিল্পের বিপনন এবং রফতানির জন্যের বিখ্যাত ছিল। বন্দরের বর্নাঢ্য জীবন যাত্রার কথা পর্তুগীজদের ইতিহাসে বর্ণিত আছে।
কাঁচপুরঃ-
শীতলক্ষ্যা নদী তীরে কাঁচপুর একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসের ধারা বিবরনীতে কাঁচপুরের সাথে জড়িত আছে ঈসাখাঁ, মূসাখাঁর স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস। কাঁচপুর মানে কাঁচকড়া কাছিমের দেহের উপরি ভাগের খোলস। একটি লোকজ শিল্পের সমৃদ্ধশালী গ্রাম হিসেবে কাছিমের খোলস কাঁচকড়া থেকে বোতামও কড়ি তৈরী করার শিল্প ছিল কাঁচপুরে। কুতুবপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জামদানী, বোতাম শিল্প বিস্তৃত ছিল। শীতলক্ষ্যার পূর্বতীর এবং পশ্চিমতীরে জামদানী ও বোতাম শিল্পের যে সুমহান অস্তিত্ব ছিল আজ তার কিয়দংশ টিকে আছে কুতুবপুর, কুড়িপাড়া, দেওয়ানবাগ, কুশাবো, সাদীপুর, পঞ্চমীঘাট, ডেমরা, তারাবো, নোয়াপাড়া এসব এলাকায়
ঝিনুক শিল্পের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম/লাঙ্গলবন্দ/অলিপুরা/মহজমপুর
নদীবিধৌত প্রাচ্যের রহস্য নগরী সোনারগাঁয়ের অমূল্য সম্পদ হলো নদ নদী, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা মেনিখালির তীরে বৈদিক যুগ থেকেই উপমহাদেশ খ্যাত লোকজ শিল্পের সমৃদ্ধ পদচারনার উম্মেষ হয়েছিল। প্রদোষকালের সেই বর্নাঢ্য লোকজ শিল্প সম্ভারের কিয়দংশ এখনো টিকে আছে। প্রাচীন কালিকাপুরান খ্যাত পরশুরামের স্মৃতি বিজড়িত হিন্দুদের তীর্থ স্থান লাঙ্গলবন্দ ঝিনুক শিল্পের গৌরবজ্জল রশ্মির শেষ রশ্মি এখনো প্রোজ্জলিত। লাঙ্গলবন্দে স্বামী বিবেকানান্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেহেরুর দেহভস্ম এখনো রক্ষিত। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এ জনপদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ঝিনুক সংগ্রহ, বাজার জাতকরন এবং ঝিনুক দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রফতানিকরন। ঝিনুক থেকে উৎপাদিত মুক্তা, বোতাম, চুন কে ঘিরে একসময় সমৃদ্ধ অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল যার রেশ ছিল গত শতাব্দির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। ঝিনুকের বোতাম, মুক্তার কথা বর্ণিত আছে চীনের মিঙ সম্রাটের ইতিহাসে। চৈনিক পরিব্রাজক কংছুলো, মাহুয়ান, ফাহিয়েন নদ নদী খাল বেষ্টিত রহস্য নগরী সোনার গাঁকে বোতাম, ছুরি, কাঁচি এবং তুলোট কাগজের উৎপাদিত শহর হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তা থেকে ধারনা করা যায় চৈনিক পরিব্রাজকরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে লাঙ্গলবন্দ, অলিপুরা, মহজমপুর, কাঁচপুর এ জনপদকে ঘিরে এ শিল্পের পদচারনা দেখেছিলেন যা তাদের ইতিহাসে তা বর্ননাও করে গেছেন। পঞ্চমীঘাট হিন্দুদের আরেক তীর্থস্থান। পশ্চিমে দেওয়ানবাগ এবং কুতুবপুরে বারো ভূইয়াদের দূর্গ ছিল এবং দেওয়ান বাগের দিঘী থেকেই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট জন স্টিপেলটন ঈসা খাঁর নির্মিত নয়টি কামান উদ্ধার করেন যা এখনও ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। ব্রহ্মপুত্র পারের সভ্যতার প্রানকেন্দ্র লাঙ্গলবন্দ, অলিপুরা ও মহজমপুর নগর বন্দরে ঝিনুক শিল্পের বড় বড় আড়ত ছিল। গত শতকের শেষ দিকেও ঝিনুক ব্যবসায়িদের পদচারনা কিয়দংশ ছিল। এখন প্রায় বিলুপ্ত। আমরাই আমাদের শেশব ও কৈশোর কালে দেখেছি ব্রহ্মপুত্রের তীরে ঝিনুকের বিশাল স্ত্তপ। এ সমস্ত ঝিনুক ফাগুন ও চৈত্র মাসে সংগ্রহ করা হতো। এবং এ ঝিনুকের মুক্তা সংগ্রাহক ছিল যাযাবর শ্রেণীর লোক প্রসঙ্গতই বেদে সম্প্রদায়। ব্রহ্মপুত্র, মেনিখালি থেকে ঝিনুক সংগ্রহের জন্যে শত শত বেদে নৌকা এ নদ নদীতে সমবেত হতো। বেদেরা উত্তরে হরিহরদি, মহজমপুর, ধন্দির নদী থেকেও ঝিনুক সংগ্রহ করে নদীর তীরে স্ত্তপকৃত করে রাখতো। সংগৃহীত ঝিনুক লাঙ্গলবন্দের আড়তদারদের নিকট তা বিক্রী করতো। আমরাও কিশোর বয়সে নদী থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে বাড়ীতে এনে তা ফাটিয়ে তার ভেতর থেকে মুক্তো আহরনের ব্যর্থ চেষ্টা করতাম।
গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকদের ঝিনুকের খোসা গুলোকে চামচ হিসেবেও ব্যবহার করতে দেখেছি। এই ঝিনুক থেকে মুক্তো আহরনের জন্য এক বিশাল পেশাদারি গোষ্ঠী গড়ে ওঠেছিল ব্রহ্মপুত্র পারের সভ্যতায়। বেদেরা ঝিনুক থেকে মুক্তো আহরন করে ঝিনুকের খোসাগুলো বন্দরে, বাজারে মহাজনদের নিকট বিক্রী করে দিত। মহাজনদের কাছ থেকে দরীদ্র লোকজন সে খোলস গুলো কিনে নিয়ে যেতো। দরীদ্র গৃহবধু ও মেয়েদের কাজ ছিল সুপারি কাটার মতো ছোরতা দিয়ে তা কেটে বোতামের আকৃতি দেয়া এবং এক প্রকারের মেসিনের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হতো। এই বোতামগুলোকে মোটা কাগজে বান্ডিলকরে স্থানীয় হাটে অথবা ঢাকার সূত্রাপুর ও সদরঘাটে বিক্রী করা হতো। সোনারগাঁয়ের ব্রহ্মপুত্রনদ অববাহিকার উৎপাদিত ঝিনুক সামগ্রীর বিশাল বানিজ্য ক্ষেত্র ছিল ঢাকার সূত্রাপুর এবং সদরঘাটে। সূত্রাপুর এবং সদরঘাট থেকে ক্রেতারা এই ঝিনুকের বোতাম সংগ্রহ করে তা ভারতের কোলকাতায় চালান করতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে এ বোতাম ভারতে পাঠানো দূঃসাধ্য হয়ে পড়ে, পরে প্লাষ্টিকের সহজলভ্য বোতাম বাজারে আমদানির ফলে ঝিনুক শিল্প চরম দুরাবস্থায় পতিত হয়। একমাত্র ঝিনুক থেকে দুর্লভ মুক্তো আহরনের পেশাদারী সম্প্রদায়ের গুটিকয় পরিবার এখনো টিকে আছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ ঝিনুক শিল্পের শৈল্পিক দিক যেমন ঝিনুকের তৈরী ফুল, লতা, পাতা, চুলের বাধুনি এ নান্দনিক শিল্পের সম্প্রসারন করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করার ফলে এ সমৃদ্ধ শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। ঝিনুকের খোসা প্রায় সবটাই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। যা পুড়িয়ে চুন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
বর্তমানে সে শিল্পও লুপ্ত প্রায়। সোনাগাঁয়ের চারু ও কারু শিল্পের বর্নাঢ্য বিকাশে ঝিনুক শিল্পের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সোনারগাঁয়ের এ শিল্পকে লুপ্তই বলা যায়।
কাপাসিয়াঃ-
শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পাড়ের গড় এলাকা। বৃহত্তর সোনার গাঁয়ের একটি লোকজ সম্পদ সমৃদ্ধ গ্রাম। চর্যাপদের বিভিন্ন দোহায় কাপাসিকার নাম বর্নিত আছে। কার্পসতুলো উৎপাদনের জন্য কাপাসিয়ার নাম একসময়ে পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। কাপাসিয়া অঞ্চলের পৃথিবী বিখ্যাত সাদা তুলো দ্বারা নির্মীত হতো সোনার গাঁয়ের ভূবন খ্যাত রমনীয় মোহনীয় মসলিন।
কুড়িপারাঃ-
শীতলক্ষ্যার নদীর সামান্য দূরে কুটিপাড়া বা কুড়িপারা দু নামেই বিখ্যাত ছিল এ স্থানটি। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এ স্থনটির নাম চার্যাপদেরএক কুড়ি নামেরও ইংগিত বহন করে। কাঁচপুরের কুড়িপারা, কুতুবপুর এসব স্থানে বোতাম, কড়ি ও জামদানী শিল্পের জন্যেও বিক্ষাত ছিল। ঐতিহাসিকগণ ধারনা করেন দেওয়ানদের চাল কুটার জন্যে যারা এস্থানে বসবাস করতো তাদের এ পাড়াকে বলা হত কুড়িপাড়া।
কুটিপাড়া ঃ-
সোনার গাঁয়ের জাদুঘরের প্রবেশের মুখে ঐতিহাসিক জনশ্রুতির ‘‘পিঠাত্তয়ালির পুল’’ সংলগ্ন এ গ্রামটি জনশ্রুতি আছে যে জনৈক পিঠা বিক্রেতার বদান্যতায় সেতুটি তৈরী হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা চাউল ও চিড়া কুটার পেশার সাথে সন্নিবিষ্ট ছিল। কাটা কুটির জন্যে এ স্থানটি বিখ্যাত ছিল বলে ‘‘কুটি পাড়া’’ চিহ্নিত হয়েছে বলে অনুমিত। বিখ্যাত পিঠাওয়ালির সেতুর নিচের স্রোতস্বিনী খালটি পানামের ইতিহাস খ্যাত ‘‘পংখিরাজ খালের’’ সাথে মিলিত হয়েছে। কুটিপাড়া গ্রামটি কেম্পানীগঞ্জ গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত। ঐতিহাসিকদের ধারনা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুরি মালামাল এ বন্দর দিয়ে রফতানির জন্যে নিয়োজিত ছিল বলেই এ গ্রামের নাম ‘‘কোম্পানিগঞ্জ’’ নামে অভিহিত ছিল।
বাড়ে মজিলিস/বাড়ে চিনিষঃ-
সুলতানি আমলে সরকারী আমলা আমত্যদের পদবি ছিল ‘‘বাড়ে মজলিশ’’ ইদানিং কালের বাড়ে মজলিশের নামকরণ করা হয়েছে ‘‘বাড়ী মজলিশ’’ নামে। বাড়ী মজলিশের প্রাচীন স্মৃতি বহন করছে কয়েকটি প্রাচীন সমাধি ও একটি মসজিদ। মসজিদের লোকজ সমৃদ্ধ পোড়া মাটির ফলক স্থানীয় মৃৎ শিল্পীদের দক্ষতাই প্রমান করে। বাড়ী মজলিশ সংলগ্ন বাড়ে চিনিষ’’ চৈনিক পরিব্রাজকদের স্মৃতিই বহন করছে। ধারনা করা হয় যে সোনারগাঁও ভ্রমনকারি চৈনিক পর্যটকেরা ‘‘বাড়ী চিনিষ’’ গ্রামেই অবস্থান করেছিলেন, সময় চতুর্দশ শতক।
খাসনগর গ্রামঃ
খাস শব্দ শ্রেষ্ঠ, আসল । সুলতানী আমলে সুলতানের চীফ সেক্রেটারিকে বলা হত ‘‘দবীর খাশ’’। সে অর্থে খাসনগর গ্রামটির বিশাল দিঘি এবং সন্নিকটস্ত প্রাচীন ইমারত প্রমান করে সোনারগাঁয়ের প্রাচীন ইতিহাসের এক সোনালী খন্ড এখানে লুকিয়ে আছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত সোনারগাঁয়ের এ দিঘীটির তীরেই পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন কারিগরদের তাঁত খানা ও আবাসস্থল ছিল। পৃথিবী খ্যাত ‘‘মলমল খাস, মলবুস খাস, জামদানী’’ সরকার-ই-আলীর সর্ববৃহৎ তাঁত খানা ছিল এ খাসনগর গ্রামে । বাহারি স্থান- গায়বিতে উল্লেখ আছে সুবেদার ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নুুরজাহানের জন্যে সোনারগাঁয়ের খাসনগর গ্রামের উৎপাদিত বিশ হাজার টাকা ‘‘মলমল খাস’’ মসলিন দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। সোনারগাঁয়ের সুবর্ণ সময়ে এক লক্ষ টাকার মসলিন সোনারগাঁয়ের তাঁত খানা হতে রপ্তানী হয়েছিল । আজ হতে দেড়শত বছর আগে জেমস টেইলর যখন সোনারগাঁও ভ্রমন করেছিলেন তখন তিনি ঈস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানির কুঠিতে দেড়শত মসলিন কারিগরের নাম লিপিবদ্ধ দেখেছিলেন। মসলিনের এই রমরমাা বানিজ্যকে উপলক্ষ করে খাসনার এবং পানামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বনিকদের আগমন ঘটেছিল। মসলিনের একচেটিয়া বানিজ্য করাত্ত্ব করার জন্যে বিদেশী বনিকদের মাঝে নীরব মসলিন বানিজ্য যুদ্ধও চলেছিল বলে ঐতিহাসিকেরা ধারনা করেন।
পানাম নগরঃ-
পানাম বাংলাদেশের চারশত বছর প্রাচীন বাংলাদেশের নগর ভিত্তীক একটি প্রাচীন নগরীর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর প্রাচীনত্ব আরো গভীর হতে পারে। ‘‘পাইনাম’’ ফার্সি শব্দ। পাইনাম থেকে পানাম। অর্থ আশ্রয়। ধারনা করা যেতে পারে ঐতিহাসিক ‘‘সড়কে-ই-আযম’’ গ্রান্ড ট্রাংঙ্ক রোডের সমাপ্তি এ পানাম নগরেই হয়েছিল। সে সুবাদে পানাম নগরী ‘‘সরকার-ই-সোনারগাঁওয়ের’’ পরগনার হেড কোয়ার্টার হিসেবে ও বিবেচিত। পানামের প্রাচীনত্ব বহন করে ট্রেজারার হাউস, সেতু, কোস্পানীর কুঠি এবং প্রাচীন বনেদি ইমারত সমূহ। সোনারগাঁয়ের নান্দনিক চারু ও কারু শিল্পের জন্যে বিখ্যাত মসলিনের আড়ং ছিল পানাম নগর। পানাম নগরের বিভাশিত বর্নাঢ্য-ইমারত সমূহ স্বাক্ষ্য দেয় একসময় সোনারগাঁয়ের অভিজাত নাগরিকদের বসবাসের কেন্দ্র ছিল। লোকজ শিল্প সমৃদ্ধ নান্দনিক ফুল, লতাপাতা সম্বলিত দেয়াল, চিত্রিত চারুতায় ভরপুর মায়াবি নাচঘরকে কেন্দ্র করে লোকজ গানের আসর বসতো। মায়াবি পর্দা দুলে ওঠার মতো মসলিনের পর্দা ঋতু ভিত্তিক বিভিন্ন পূজো উৎসবে মূখর নগরী আবহমান বাংগালির লোকাচার, জীবনাচার, আবহমান জীবন সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল ছিল পানাম নগর। লোকজ উপাদানের মোটিভ সম্বলিত একচালা দোচালা ছনের ঘরের মডেল সম্বলিত ইমারত, বঙ্গীয় ‘‘একচালা দোচালা গৃহায়ন’’ সংস্কৃতির আদল রূপে সুদূঢ় দিল্লীতে সমাদৃত হয়েছিল এ থেকে কী আমরা ধারনা করতে পারিনা প্রাচীন এ সোনারগাঁয়ের ছনে ছাওয়া কুড়ে ঘরের আদলই মোগল শিল্পকলাকে উৎসাহিত করেছিল। এসবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সোনারগাঁয়ের পৃথিবীখ্যাত নান্দনিক চারু ও কারুশিল্পর জন্যে।
গোয়ালদি ঃ-
গোয়ালদি মানে গোপালক, গোয়ালাদের স্থান। ঐতিহাসিক পানাম নগরের সন্নিকটস্থ গোয়ালদি গ্রাম ঐতিহাসিক স্মৃতিবহ। এ গ্রামেই আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের মসজিদ (১৫১৯খৃঃ) আছে। তার সংলগ্ন আঃ হামিদ বাঙ্গালের স্মৃতি বিজড়িত মোগল পিরিয়ডের একটি মসজিদ ও সমাধি আছে। বাংগালির চিরায়ত রসনাজনক খাবারের উপাদান মিষ্টান্ন, দধি, মিষ্টির বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল বলে গোয়ালদী গ্রামে অনুমিত হয়।
গোয়ালপাড়াঃ-
বারদী ইউনিয়নের একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ গোয়ালপাড়া। গোয়ালা ও ময়রাদের পল্লি ছিল বলেই হয়তো এই গ্রামের নাম হয়েছে গোয়াল পাড়া।
গোবিন্দপুর ঃ-
ঐতিহাসিক মহজমপুরের নিকটবর্তী গ্রাম গোবিন্দপুর। এ গ্রামের নিকটবর্তি নদ ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ থেকে আবিস্কৃত হয়েছে মোয়াজ্জমাবাদ টাকশালের নামোল্লিখিত রাজা গনেশ এবং গিয়াস উদ্দিন আযম শাহে্র মুদ্রা।
শাহ্চিল্লাপুরঃ-
সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের অনুপম পাথরের টেরাকোটা সমাধিটি মধ্যযুগের একটি সমাধি শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। পাথরের টেরাকোটায় অলংকৃত রয়েছে গ্রাম বাংলার লোকজ সম্পদের অনন্য নিদর্শন। নিদর্শনে অঙ্কিত রয়েছে ঝুলন্ত পাটের শিকায় মাটির ছোট্ট হাড়ি। অনেকে মনে করেন এটা ঝুলন্ত মোমদান। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা মনে হয়েছে পাটের শিকায় মাটির হাড়ি।
টাটকিঃ-
স্থানীয় নাম টাইটকা। শীতলক্ষ্যা তীরের এ স্থান থেকে একটি খাল বালিয়া পাড়ার নিকটে গিয়া শীতলক্ষ্যার সঙ্গে বহ্মপুত্রের সংযোগ সাধন করেছে। টাটকির মিহি চিড়া একদা বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। অনুমান করা হয় সংস্কৃত তত্বকী, তাতাকি থেকে টাটকি হয়েছে।
তারাবঃ-
ডেমরার সন্নিকটে শীতলক্ষ্যার তীরে বিখ্যাত বানিজ্যিক এলাকা। স্থানটি বহু পূর্ব থেকেই সোনারগাঁও অঞ্চলের বিখ্যাত সূতিবস্ত্র, জামদানী, শাড়ী, মশারি, পর্দার কাপড় বিপননের জন্যে বিখ্যাত। বর্তমানে এ জমজমাট আড়ংটির এখনো অস্তিত্ব আছে।
ডেমরাঃ-
স্থানটি মোগল অফিসার কর্তৃক আবিস্কৃত। মোগল তারও পূর্বে সুলতানী আমলে এখানে নদীর গভীর খাত বা প্রবাহ ছিল। গভীর খাত থেকে তটভূমি বা বালিয়ারির খোঁজ করতে গিয়ে নৌবহরের কে একজন বলে ওঠেছিলেন ‘‘ডেওরা’’ হাতের বা দিকে, নলিনী কান্ত ভট্টশালী ‘‘ বেঙ্গল চীফস স্ট্রাগল’’ গ্রন্থে ডেমরার শীতলক্ষ্যা নদীতে বেদেদের বিশাল বহরের উপস্থিতির কথা বলেছেন। ডেমরার শীতলক্ষ্যা নদীতে বর্তমানেও বেদেদের কিয়দংশের অস্তিত্ব আছে।
নারায়ণগঞ্জঃ-
ব্রিটিশ ও পাকিস্তান পিরিয়ডের প্রথমার্ধে নারায়ণগঞ্জ শহর ছিল মহকুমা শহর। স্বাধীনতার পর নারায়ণগঞ্জ জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রিটিশ পিরিয়ডের শেষের দিকে পানামের নারায়ণ পোদ্দার ছিলেন নারায়ণগঞ্জের প্রথম মেয়র। পাট এবং পাট জাত দ্রব্যাদির জন্যে সারা পৃথিবীতে নারায়ণগঞ্জের পরিচিতি ছিল প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে। বলতে গেলে তদানিন্তন পাকিস্তানের মূল অর্থনীতিই আবর্তিত হতো বৃহত্তর সোনারগাঁয়ের নারায়ণগঞ্জের অঞ্চলের পাট জাত দ্রব্যাদির অর্থ থেকে। ঈসাখাঁর আমলের স্মৃতি বিজড়িত নারায়ণগঞ্জ শহরে ঈসাখাঁর নামে একটি রাজপথের নামকরন করা হয়েছে। মোগল পিরিয়ডের একটি দূর্গ নারায়ণঞ্জের ঐতিহ্য প্রকাশ করছে।
চরলালঃ-
সোনারগাঁয়ের কার্পাস শিল্পের পর সোনারগাঁওয়ের সনমান্দী ইউনিয়নের চর লালের বগি পাটের উজ্জলতা এবং দীর্ঘ আশেঁর জন্যে তৎকালিন পাকিস্তানে এক বিরল বৈশিষ্ট অর্জন করে।
বারদীঃ-
শব্দটি হলো বাহারদি। নদী থেকে ভেসে ওঠা একটি চর। বাহারদি থেকে বারদী নামের উৎপাত্তি হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন। একসময়ের সূতো, তাঁত, থানকাপড় এবং লুঙ্গি ও গামছার জন্যে বারদী বিখ্যাত ছিল। বারদীতে ছিল বিখ্যাত স্টীমার ঘাট। আজকে আমরা টেলিগ্রাফের যে খুঁটি দেখি, উল্লেখ থাকে যে বারদীর সমৃদ্ধ ব্যবসা বানিজ্যের জন্যেই এ টেলিগ্রাফ সংযোগের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সর্বভারতীয় নেতা শ্রী জ্যোতিবসুর পেত্রিক বাসস্থান এবং সাধক শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম হিসেবেও উপ-মহাদেশে বারদীর ব্যাপক পরিচিতি আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এন.সি.নাগ বারদির বিখ্যাত নাগ পরিবারের সন্তান।
একসময়ে দেশীল ফলের বাগানে ভরপর ছিল সোনারগাঁও। বিশাল আমবাগানের জন্যে আমবাগ গ্রামের পত্তন হতে পারে বলে অনেকে ধারনা করেন।
মদনগঞ্জঃ-
নারায়ণগঞ্জের বন্দরের নিকটবর্তী মদনগঞ্জ একসময় চাউলের আড়ত এবং কাঠের জন্যে বিখ্যাত ছিল। ১৫৮৬ খ্রীঃ ব্রিটিশ রানী এলিজাবেথের বিশেষ দূত রালফ ফীচ যখন সোনারগাঁও ভ্রমন করেন, তিনি সোনারগাঁও বন্দর ও মদনগঞ্জের আশপাশ থেকে প্রচুর চাল সুমাত্রা, জাভাতে রফতানি হতে দেখেন। তখন সোনারগাঁয়ে ঈসাখাঁর রাজত্বকাল।
মরিচ টেকঃ-
এক সময়ে হয়তো এখানে মরিচ বেশী হতো। সম্ভবত এ কারণে হয়তো এই টেকের নাম মরিচটেক নামকরন করা হতে পারে।
লাঙ্গলবন্দ এবং পানামের আশপাশের স্থানগুলোতে একসময় কাঠের হাতি এবং ঘোড়া নির্মানের কারিগরদের বাসস্থান ছিল। হিন্দু পুরানের মতে গৌড়ের রানী সোনরগাঁয়ের কাঠের ঘোড়া এবং হাতির জন্যে বায়না ধরেছিলেন। রানীর সখ মেটাতে পুরানে উল্লেখ আছে কাঠের ঘোড়া এবং হাতি সুবর্ণগ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাঠের ঘোড়া এবং হাতির কারিগরের শেষ বংশধর মনীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর এখনো বসবাস করছেন। সোনরগাঁয়ে। বাঁশ এবং বেঁত শিল্পের জন্যে বিখ্যাত ছিল সোনারগাঁও। এখনও সোনারগাঁয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোর দরীদ্র গৃহবধূরা বেতের মোড়া এবং বাঁশ নির্মীত ডুলা, ওছা, নির্মান ও তা বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করছে।
উপরিউক্ত গ্রামের নামগুলোর পাশাপাশি সোনারগাঁয়ের অনেক গ্রাম রয়েছে যে গ্রামগুলোতে লুকিয়ে আছে সোনারগাঁয়ের প্রাচীন ইতিহাসের পাশাপাশি বর্নাঢ্য লোকজ সম্পদ। যা বিলুপ্তির পথে বা অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে। এর সার্বিক ধারনা দিতে হলে বিস্তৃত কলেবরের প্রয়োজন। যৎসামান্য এ লেখার মর্মার্থ উপলব্দি করে গবেষকরা এগিয়ে যাবেন, প্রজন্মের কাছে এটুকুই আমার প্রত্যাশা।
সংগ্রহে- শামসুদ্দোহা চৌধুরী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস